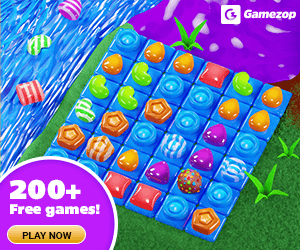Bangla News Dunia, বাপ্পাদিত্য:- বাংলাদেশে আসলে হচ্ছেটা কী? এ পারের টিভি চ্যানেলগুলো বলে চলেছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের জীবন বিপদগ্রস্ত। মূলত হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলেও অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও বাদ নেই। আবার বাংলাদেশের মাটিতে শোনা গেল কলকাতা দখলের ডাক। শুধু মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের আমলে নয়, শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়া— সব আমলেই কমবেশি সংখ্যালঘুরা লাঞ্ছিত, সংবাদসূত্র এমনই বলছে।
একটি কোটা-বিরোধী আন্দোলন রূপান্তরিত হল ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে। শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, ছাত্রনেতাদের কেউ কেউ হয়ে গেলেন সরকারের উপদেষ্টা আর মসনদে বসেই তাঁরা বিষোদ্গার করে চললেন ভারতের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে আমার অগণিত সজ্জন বন্ধু আছেন। তাঁরা প্রতিনিয়ত বলে চলেছেন সব ধর্মের প্রতি সহনশীলতার কথা। আমার মনে হয়, এই সজ্জন মানুষেরর সংখ্যাই বেশি কিন্তু মৌলবাদীরা যদি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তারা সংখ্যায় কম না বেশি, সেই পরিসংখ্যান বড় কথা নয়, তাদের কুকর্মের ব্যাপ্তি অনেকটাই আর এটাই হচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে।
সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সব থেকে অপ্রত্যাশিত ঘটনা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সখ্যের ঢক্কানিনাদ। ইউনূস সরকারের আমলে পঞ্চাশ বছর বিরতির পর চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর ফেলেছে পাকিস্তানের বাণিজ্য জাহাজ। পাকিস্তানের নতুন ভিসা নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়া পাকিস্তানে যাতায়াত করতে পারবে। পাকিস্তানের জনৈক ধর্মীয় নেতা হুঙ্কার দিয়েছেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত হাত ওঠালে পাকিস্তান দেখে নেবে, তিনি বাংলাদেশিদের সম্বোধন করেছেন ‘ভাই’ বলে। আহা, কী ভ্রাতৃত্বের সুরবন্ধন!
বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম জানে কি, একাত্তরে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার এবং রাজাকারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খান সেনারা কী করেছিল? যেটুকু আন্তর্জাতিক রাজনীতি বুঝি, তার প্রেক্ষাপটে বলতে পারি শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার যথেষ্ট ভ্রান্তি আছে। শেখ মুজিবকে যে ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, একই প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল তাজউদ্দিন আহমেদকে। শেখ মুজিব কিংবা শেখ হাসিনা, কেউ সেটা দেননি। তা ছাড়া হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে, তবে এই নিবন্ধে এ সব বিষয় থেকে সরে গিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব কেন বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে সখ্য হতে পারে না। এই বিষয়টির পক্ষে যুক্তি রাখতে শিশু-অধিকার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব।
‘যুদ্ধশিশু’ কিংবা ‘ওয়ার চিল্ড্রেন’ কথাটার সঙ্গে, বাংলাদেশের নবীন প্রজন্ম, বিশেষত যাঁরা ছাত্র আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে ইউনূস সরকারের উপদেষ্টা মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছেন তাঁরা পরিচিত কি? ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের টালমাটাল সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার পর বাংলাদেশি নারীরা যে সকল শিশুর জন্ম দেন, তাদের যুদ্ধশিশু রূপে চিহ্নিত করা হয়। এদের পরিচয় ছিল ‘অবাঞ্ছিত শিশু’, ‘শত্রু সন্তান’, ‘অবৈধ সন্তান’, এমনকী আরও অবজ্ঞাভরে বলা হত পিতৃ পরিচয়হীন ‘জারজ সন্তান’। সমাজে কলঙ্কের ভয়ে অনেক জন্মদাত্রী মা আত্মহত্যা করেন, অনেকে গর্ভপাত ঘটাতে কিংবা জন্ম দিতে স্থান ত্যাগ করে চলে যান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশের কতজন মা-বোন এই দুর্গতির শিকার হন, সে বিষয়ে সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী কালে বিভিন্ন এনজিও-র রেকর্ডপত্রে এবং বিদেশি মিশনারি সংস্থাগুলোর নথিপত্রে যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে সীমিত হলেও বেশ কিছু দস্তাবেজ পাওয়া যায়।
একটি ইতালীয় চিকিৎসক দলের সমীক্ষা অনু্যায়ী, যুদ্ধশিশু জন্মদানকারী মহিলাদের সংখ্যা ৪০ হাজার বলা হয়েছে। আবার ব্রিটিশ সংস্থা ‘ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড পেরেন্টহুড ফেডারেশন’-এর হিসাব অনুযায়ী, এই সংখ্যাটি দু’লক্ষ। ওই সময়ে যুদ্ধশিশুদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সমাজকর্মী জিওফ্রে ডেভিস বলেছিলেন, এ সংখ্যা হয়তো আরও অনেক বেশি হতে পারে। কতজন নির্যাতিতা মহিলার গর্ভসঞ্চার হয় এবং কতজন সন্তানের জন্ম হয়, সে সংখ্যাটি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তবে পাকিস্তানি দুর্বৃত্তদের হাতে ধর্ম নির্বিশেষে মা-বোনেরা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।
ওই সময়ের সংবাদপত্রে যুদ্ধশিশুদের নিয়ে যত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ডের সভাপতি বিচারপতি কেএম সোভান, মিশনারিজ় অব চ্যারিটি-র সিস্টার মার্গারেট মেরি এবং জিওফ্রে ডেভিস, ওডার্ট ফন শুল্জ় প্রমুখের সাক্ষাৎকারও ছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সব সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, স্থানীয় বাঙালি চিকিৎসকদের সহায়তায় ব্রিটিশ, মার্কিন ও অস্ট্রেলীয় চিকিৎসকদের একটি দল ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ২৩ হাজার নির্যাতিতা মহিলার গর্ভপাত করেন। এর পর বিদেশ থেকে চিকিৎসক দল বাংলাদেশে আসতে শুরু করেন। তাঁরা ঢাকায় গর্ভপাত করানো বা সন্তান জন্মদানের জন্য ‘সেবা সদন’ নামে পরিচিত বেশ কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সংবাদসূত্র অনু্যায়ী, দেশব্যাপী স্থাপিত একাধিক সেবা সদনে কয়েক হাজার শিশুর জন্ম হয়েছিল। ক্যানাডার ইউনিসেফ কমিটির তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ ও যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার সফর করেন। এ সফরকালে ঢাকায় ইউনিসেফ-এর কর্মকর্তা এবং লিগ অব রেডক্রস সোসাইটিজ়-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর কয়েক বার আলোচনা হয়। এ আলোচনার পর তিনি অটোয়ায় সদর দফতরে যে প্রতিবেদন পেশ করেন, তাতে বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুর সংখ্যা দশ হাজারের মতো বলে উল্লেখ করা হয়।
এই লাঞ্ছিত মা ও সন্তানদের জন্য সর্বপ্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার করে, তা হল ১৯৭২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড গঠন। বাংলাদেশে যে সব মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, তিন থেকে চার মাসের মধ্যে তাঁদের সবার কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া ছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্যটি ছিল, অসংখ্য নির্যাতিতা মহিলার দ্রুত কার্যকরী পুনর্বাসনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা, কর্মসূচি গ্রহণ ও তার রূপায়ণ। নির্যাতিতা মহিলাদের মধ্যে স্রেফ ধর্ষিতা রমণীরাই ছিলেন না, তাঁদের অনেকেই ছিলেন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ, পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তাঁদের স্বামী নতুবা পিতা কিংবা ভাইয়ের মতো কোনও উপার্জনশীল নিকটজন নিহত হয়েছেন অথবা যুদ্ধে তারা সহায়-সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।
শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অনুরোধে প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসে, সেটি হল জেনেভা-কেন্দ্রিক ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস-এর যুক্তরাষ্ট্র শাখা। দু’টি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সেন্ট্রাল অর্গ্যানাইজ়েশন ফর উইমেন রিহ্যাবিলিটেশন এবং বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে।
বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের দত্তক গ্রহণের ব্যাপারে ক্যানাডাই প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দু’টি ক্যানাডা-র সংগঠন দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। এই সংগঠন দু’টির একটি হচ্ছে মন্ট্রিয়ল-এর আন্তঃদেশীয় দত্তক সংস্থা ‘ফ্যামিলিজ় ফর চিলড্রেন’ এবং অন্যটি টরন্টো-র ‘কুয়ান-ইন ফাউন্ডেশন’। পরবর্তী সময়ে যে সব দেশ এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়া। বিদেশি নাগরিকরা যাতে যুদ্ধশিশুদের সহজে দত্তক নিতে পারে, সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু আদেশ, ১৯৭২ নামে একটি রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করা হয়। যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের একটি বিতর্কিত দিকও ছিল। পশ্চিমের দত্তক-গ্রহণকারী সংস্থাগুলো যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনে বেশ আগ্রহ দেখায়, কিন্তু তাদের জন্মদাত্রী মায়েদের পুনর্বাসনে তেমন আগ্রহ দেখায়নি।
আরও একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের করাচি-সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫ লক্ষ বাঙালি বসবাস করে, যাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না পাকিস্তান। ৫০ বছর ধরে বসবাস করলেও কোনও জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে শুরু করে স্কুল কলেজে ভর্তি হতেও বিড়ম্বনায় পড়ে তারা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এমন বৈষম্যের শিকার এ সব পাকিস্তানি বাংলাভাষীরা।
আশা করি, ভারতের সঙ্গে বৈরিতা করে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আগে এই যুদ্ধশিশু এবং লাঞ্ছিতা মায়েদের কথা বাংলাদেশ মনে রাখবে। মনে রাখবে যে, এখনও পাকিস্তান কিন্তু ক্ষমা চায়নি বাংলাদেশের কাছে, বিগত শতকের এক জঘন্য যুদ্ধাপরাধের জন্য।
লেখক বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির শিশু সুরক্ষা, অ্যাডভোকেসি এবং মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান। মতামত ব্যক্তিগত